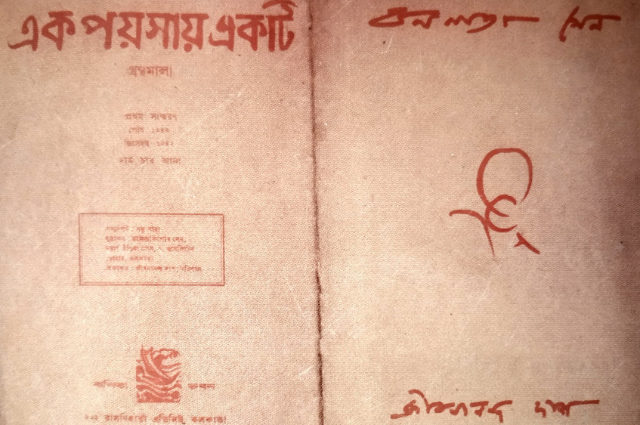।।এক।।
যুগ বিভাজন নিয়ে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম বই চর্যাপদ থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-পরবর্তী আধুনিক যুগের বিস্তৃত পরিধি পর্যন্ত আঙ্গিক, বিষয়বস্তু এবং প্রেমের প্রকাশভঙ্গিতে একটা ধারাবাহিক ক্রমবিকাশকে বরণ করে নিয়ে বাংলা ভাষার কবিরা কবিতাকে নব জন্ম দিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন। ছন্দ ও অলংকার শাস্ত্রের বোধিবৃক্ষ তাদের বৈদগ্ধে নিত্য নতুন শাখা প্রশাখা বিস্তার করে বাংলা কাব্যকে বৈভবশালী করেছিল এ কথা সত্য। এবং এটাও সত্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই প্রথম প্রচলন করেছিলেন গদ্য কবিতার। যেটা ইংরেজিতে করেছিলেন ওয়াল্ট হুইটম্যান । রবীন্দ্রনাথ শুধু গদ্য কবিতাই প্রচলন করেননি; তার স্বপক্ষে মাধুর্য
এবং বক্তব্য উপস্থাপনার কৌশলগত দিক আলোচনা করে প্রকারান্তরে পরবর্তী লেখকদের মনোযোগও আকর্ষণ করেছেন। এরপরেও যখন রবিকিরণে ভারত তো বটেই আসমুদ্র হিমাচল সুস্নাত, সেই সময় রবি-রশ্মি থেকে মুক্তি-প্রত্যাশী কল্লোল, কালি-কলম গোষ্ঠী সহ অন্যান্য কবিরা আরো বেশি স্বাতন্ত্র পরিস্ফুটনে আগ্রহী হলেন। এদের মধ্যে দুর্বোধ্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিদ্রোহী নজরুল, ধূসর জীবনানন্দ, দুর্বার বিষ্ণু দে, বামাচারী অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, উদ্দাম প্রেমেন্দ্র মিত্র, নম্র অজিত দত্ত প্রমূখ অনেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্ষোভ, যন্ত্রণা, প্রেম ও আদিমতবাদের দহন নিজেদের ধমনীতে বহন করে পরবর্তী বাঙালি কবিদের শিরায় শিরায় সেই ঐতিহ্য সঞ্চালন করতে পেরেছিলেন। ছন্দ, উপমা,অলংকার প্রভৃতি একেবারেই বাদ পড়েছে একথা বলা চলে না। তবে ব্যাপক অর্থে এরা সবাই গদ্যকবি। আধুনিক কবিতা হিসেবে চিহ্নিত এইসব কবিরা ক্রমশ আমদানি করলেন কবিতায় দুর্বোধ্যতার। সেই সময়ের মননশীল সুধীন্দ্রনাথ দত্ত নিজেই লিখেছেন তার 'স্বগত' গ্রন্থের 'কাব্যের মুক্তি' প্রবন্ধে
:এখনকার কবিতা দুর্বোধ্য। কিন্তু দুরুহতার দুটো দিক আছে একটা পাঠকের দিক, অন্যটা লেখকের। যে দূরূহতার জন্ম পাঠকের আলস্যে তার জন্য কবির উপরে দোষারোপ অন্যায়..... কিন্তু যে দূরূহতার উৎপত্তি অনুকম্পার অভাবে যার মূলে কবির নিজের দ্বিধা নিহিত, তার কতকটা যুগসন্ধির ফলাফল বটে, তবু অধিকাংশের জন্য কবিই দায়ী। দুর্বোধ্যতার স্বপক্ষে আধুনিকদের যুক্তি : জীবন যেখানে জটিল এবং সাহিত্য যেখানে 'জীবন দর্পণ' সেখানে দুর্বোধ্যতা তো থাকবেই। কবিতা তো সাহিত্যেরই অংশ।।এ কথার মান্যতা অস্বীকার করার তো উপায় নেই। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের এই আশঙ্কাও অমূলক বলে প্রমাণিত হয়নি; "কাব্য কেবল তখনই অমর পদবাচ্য যখন তার সন্ধান প্রতর্ক ছাড়িয়ে পৌঁছায় প্রমিতিতে। এই ঊর্ধ্বতন, আধুনিক কাব্যে দুর্লভ, এবং অন্তত আমার মনে এমন আশা নেই যে এদিক থেকে সে কখনো লব্ধকাম হবে।"
তারপর এল অত্যাধুনিক কবিতার জোয়ার। অনেকটা স্থিতপ্রজ্ঞ ভাব নিয়ে তারা সপ্রশংসভাবে বাংলা কবিতার জয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছিলেন বটে। কিন্তু পরবর্তীকালের সাম্প্রতিক এবং অতি সাম্প্রতিক কবির মধ্যে বাংলা কাব্যের আধুনিক যুগ থেকে এই অব্দি পর্যন্ত যারা অকবি তাঁদের বাদ দিয়ে সবাই একটা কথা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন : 'Close thy Byron , open thy Goethe' -- যুগ পরিবর্তনের ঘোষণা করতে গিয়ে কার্লইলের এই তারস্বরে গলা মেলানোর কথা তারা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না ( Sartor Resartus -- Carlyle Book II Chapter IX)।
।। দুই।।
'নতুনের আবির্ভাব চকিতে ঘটে কিন্তু কাব্যে তার প্রকাশ ধীরগতি '। এই অতি সহজ সরল উক্তিটিকে তারা গ্রাহ্যও করেন না। অথচ 'প্রেম' নিয়ে লিখতে সবাই পারঙ্গম।
'কে বুঝাইয়া দিবে যে জগত কেবল স্তুপাকৃতি কতগুলো বস্তু নহে। উহার মধ্যে ভাব বিরাজমান?
আর কেহ নহে। প্রেম। যে জগতকে ভালোবাসে সে কখনো মনে করিতে পারেনা যে জগত জড়পিন্ড। সে ইহার মধ্যে অসীমের ও চিরজীবনের আভাস দেখিতে পায়।'( ডুব দেওয়া -- ভারতী,১২৯১) উদ্ধৃতি: বাংলা কবিতার নবজন্ম -- সুরেশ চন্দ্র মৈত্র।
বাংলা কাব্য ও সাহিত্যের বিভক্ত সমালোচকদের
বক্তব্যের উপরোক্ত সারমর্মে আমার সজ্ঞান সংযোজন : বাংলা সাহিত্যের আদ্যোপান্ত ইতিহাসে 'প্রেম' কোনো কলাকৈবল্যবাদী চিন্তাধারায় আশ্রিত নয় বরং 'যাহা নিত্য, চিরসত্য, অতীতে ছিল, বর্তমানে আছে, ভবিষ্যতেও থাকিবে' জাতীয় সনাতন উপলব্ধিরই স্বীকৃতি।
বক্ষমান প্রবন্ধে 'বনলতা সেন' কে সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমের কবিতা হিসেবে বলতে গিয়ে এরকম একটা অনুভূতিক জ্ঞানের আশ্রয় নেয়াটা আবশ্যিক। একইসঙ্গে এটাও বলতে হবে আমাকেই : যারা কবিতা লেখেন, তাদের ' সকলেই কবি নন কেউ কেউ কবি.... কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায় জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মুষিকাঞ্জলীর ভেতর শালিকের মতো স্নান না করে বরং যেন
করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের সাদা রৌদ্রের মতো'। সৎ কবি ও কবিতার সংজ্ঞা নিরূপণে এমন কঠোর উক্তি যিনি করেছিলেন তিনি জীবনানন্দ দাশ। এবং আশ্চর্য এখন পর্যন্ত তিনি অননুকরণীয়, ভাবে এবং প্রকাশে- যিনি 'রূপসী বাংলা'র বনলতা সেনের প্রেমিক কবি। অতি সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত একশ্রেণীর কবিদের মেজাজের রুক্ষতা,বক্তব্য নির্বাচন এবং প্রকাশভঙ্গিতে অকাব্যিকভাবের কথা বিবেচনা করে উক্তিটির অর্থবহতা সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ। এবং তারই কবিতার শ্রেষ্ঠ কথা 'বনলতা সেন' একটি অপূর্ব প্রেমের কবিতা।
একটা চিঠিতে তিনি লিখছেন নিজের সম্পর্কে, "একদিনের কথা: আষাঢ় এসে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু বর্ষণের কোন লক্ষণ দেখছি নে। মাঝে মাঝে নিতান্ত " নীলোৎপলপত্রকান্তিভি: ক্কচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈ:" মেঘমালা দূর দিগন্ত ভরে ফেলে চোখের চাতককে দুদন্ডের তৃপ্তি দিয়ে যাচ্ছে।
তারপরেই আবার আকাশের ceruclean vacancy, ডাক-পাখির চিৎকার, গাংচিল-
শালিকের পাখার ঝটপট, মৌমাছির গুঞ্জরন- উদাস অলস নিরালা দুপুরটাকে আরও নিবিড়ভাবে জমিয়ে তুলচে।
চারদিকে সবুজ বনশ্রী, মাথার উপর সফেদ মেঘের শাড়ি, বাজ পাখির চক্কর আর কান্না। মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির সবজি বাগের ভেতর বসে আছি, দূরে-দূরে তাতার দস্যুর হুল্লোড়। আমার তুরানি প্রিয়াকে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি!.... হঠাৎ কোত্থেকে কত কি তাগিদ /এসে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় একেবারে বেসামাল বিশমিল্লাহর ভিড়ে! সারাটা দিন- অনেকখানি রাত- জোয়ার ভাটায় হাবুডুবু!"
।। তিন।।
'প্রেম জীবনকে দেয় ঐশ্বর্য, মৃত্যুকে দেয় মহিমা। কিন্তু প্রবঞ্চিত কে দেয় কি? তাকে দেয় দাহ' (দৃষ্টিপাত -- যাযাবর )। এই প্রেম সে প্রেম নয়। এটা অকৈতব প্রেমলীলা অথবা রাধাদাস্যও নয়। অবশ্যই আমার দাবির সমর্থনে মনে রাখতে হবে, বনলতা সেন ইতিহাস আশ্রিত কোন প্রেম কাহিনীর নায়িকা নয়, কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'নুরজাহান'
নয়। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মানসী'ও নয়। এ প্রেম অতীন্দ্রিয় ভাববিলাসী প্রেমও নয়। বরং এটা হল একটা যান্ত্রিক যুগ তথা আজকের ডিজিটাল যুগের এক মহিলার করুণাঘন প্রেম -- যা প্রেমিককে হতাশার নশ্বর উপকূলে না নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে চিন্ময় চেতনার এক বিস্ময়কর মিলন প্রান্তে পৌঁছে দেয়। প্রেমের শূন্যতাবোধই বিরহের হাতছানি এবং দুর্বহ পথে চলার প্রারম্ভিকী আমার হৃদয়ে যেমন জাগিয়ে তোলে এক অন্তহীন বেদনার অনুভূতি তেমনি সমস্ত জীর্ণতা, বিষন্নতা পথের ক্লান্তি, পারিপার্শ্বিক ধূসরতা অতিক্রম করে আমাকে সন্ধান দেয় এমন এক নির্জন জগতের যেখানে শুধুই প্রেম, নিখাদ প্রেম, যেখানে শুধু তুমি আর আমি আর ক্ষনিকের প্রগাঢ় প্রশান্তি। এ এক স্বর্গীয় জগত। যেখানে কামনা বাসনার নেই কোন স্থান। এখানে স্থানীয় এক স্বাভাবিক নারী তার লজ্জা,ভীরুতা, কমনীয়তা নিয়ে চিরন্তন সৌন্দর্য ও শাশ্বত প্রেমের আধার হিসেবে উপস্থিত। সত্যিই তো "আমি ভালোবাসি যারে সে কি কভু আমা হতে দূরে যেতে পারে?" একই সাথে স্বর্গের উর্বশী এবং বাংলার এক পালিশড নারী হিসেবে 'এই বনলতা
সেন'ই চিরকালের এবং অখন্ড মানুষ ' ( চর্যাপদ -- অতীন্দ্র মজুমদার )।"একজন যায়,আরেকজন আসে। যে যায় সেও নিশ্চয়ই কোথাও গিয়ে উপস্থিত হয়। আর যে আসে, সেও হয়তো কত অজানিত দেশ ঘুরে কত অপরিচয়ের আকাশ অতিক্রম করে একেবারে হৃদয়ের কাছটিতে এসে দাঁড়ায়:" এইতো বনলতা সেন। বিস্ময় বিমুগ্ধ অন্তরে আমি তাই তাকিয়ে থাকি বনলতার মুখের দিকে আর মনে মনে আঁকতে চেষ্টা করি তার মুখের আদল। আমি তাই ভালোবাসি বনলতা সেনকে। প্রেমের রহস্য সবসময়েই অতিলৌকিক বা অলৌকিক নয়, এমনকি নয় অতীন্দ্রিয় ও। তথাপি এটা অব্যাখ্যাতই থেকে যায়। তার কারণ এটা হৃদয়ের একটা অনুভূতির বিষয়। অযৌক্তিক ভাব বিলাসিতাকে আশ্চর্যজনকভাবে পরিহার করে চিত্তাকর্ষকভাবে এই বিষয়টিই এই কবিতায় বিধৃত। প্রত্যেকটি পুরুষ বা নারীর প্রেমময় উপস্থিতির স্বতঃসিদ্ধতা প্রকাশ করে এই কবিতা। অপ্রেমিক আছে কিনা জানা নেই তবে অপ্রেমিকরা চিরকালই অমানুষ- একথা স্পর্ধা ভরে উচ্চারণ না করেও আমি বলতে পারি - - যুগ যুগান্তর ধরে
বাস্তবিক পক্ষে 'প্রেম' বলতে যা বোঝায় এখানে তারই উজ্জ্বল প্রকাশ। এটা হৃদয়ের সেই প্রেম, যার হাত ধরে আমরা চিনতে পারি আমাদের নিজস্ব হৃদয়ের প্রেম কি এবং প্রেমিক বা প্রেয়সীকে, মা কে। আমার প্রাগুক্ত ভূমিকাকে প্রেক্ষাপটে রেখেই 'বনলতা সেন' আমার কাছে অনবদ্য একটি প্রেমের কবিতা এবং আমার প্রিয়তম কবিতা। আমি তন্ময়-আবৃত চিত্তে আমি যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি এই মনলালিতা যুগলবন্দীর চিরস্থায়ী উপস্থিতি।
।। চার।।
এই কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের অর্থ,ব্যাখ্যা, টিকা- টিপ্পনি, রূপকতা, ছন্দ,চিত্ররূপময়তা, ইতিহাস-তন্ময়তা, এডগার এলেন পো, ইয়েটস, টি,এস, এলিয়ট, পি, বি, শেলী প্রমুখ কবিরা কেমন করে প্রভাবান্বিত করলেন জীবনানন্দকে এই কবিতায়, বনলতা সেন নাম্নি এই নারীর পরিচয় কি এসব বিষয় নিয়ে অনেক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা- সমালোচনা হয়েছে। জীবনানন্দের মাতা কুসুম কুমারী দাসের লেখা কবিতা, ' আদর্শ ছেলে' নামক
কবিতা এখনো আদর্শ স্থানীয় কবিতা এবং সুখপাঠ্য। বাংলা ভাষায় একটা কবিতা 'বনলতা সেন' কে নিয়ে নিয়ে এত হইচই এত আলোড়ন এর আগে হয়নি। অনুবাদের সংখ্যা ও প্রচুর। লেখকের স্বকৃত অনুবাদও আছে। বিতর্কের ঊর্ধ্বে যেসব শিল্পীর অবাধ বিচরণ তাঁদেরও অনেকেই বনলতা সেনের ছবি এঁকেছেন। যে কোন মহৎ ভাস্কর্যের আবেদন যেমন চিরকালের, তেমনি জীবনানন্দের ধ্রুপদী ভাস্কর্য 'বনলতা সেন' এর ও। সব আলোচনা সমালোচনাকে প্রসঙ্গে টেনে না এনে আন্তরিক অভিব্যক্তিমুখর আমি- আমার দৃপ্ত কণ্ঠস্বর 'বনলতা সেন' একটি প্রেমের কবিতা এবং আমার প্রিয়তম কবিতা।
এর অর্থ এই নয় যে, জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কিত সব আলোচনা- সমালোচনাই আমার অধীত। তবে নূন্যতম পক্ষে আমি এটুকু সদম্ভে উচ্চারণ করতে পারি- কবি জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তো বটেই, তাঁর তিরোধানের পরেও তিনি যতটুকু নিন্দিত হয়েছেন- তার চাইতে ঢের বেশি প্রশংসিত হয়েছেন প্রতিষ্ঠিত সমালোচকদের দ্বারা। 'হাজার বছর ধরে' 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'এই অতি পুরনো
শব্দবন্ধন গুলো সহ গোটা কবিতাটিরই যে বক্তব্য তা আমার মনে হয় একটা চিরকালের আবহমান কন্ঠস্বর। কিন্তু কবি ও কবিকৃতির যে শূন্যগর্ভ সমালোচনাটিকে আমি পাশ কাটিয়ে যেতে পারিনি, তা একটু উপস্থাপিত করছি : '.....প্রথমে কবির দূর-কালে এবং দূর -অতীতে দেশে দেশে পথচলা। তার যে কোনো লক্ষ্য আছে, তার মধ্যে যে বিশেষ কোন সন্ধান আছে ( অনেকে কল্পনা করে নেন কাম্য রমণী বনলতার খোঁজেই যেন এই দ্বিমুখী স্থানে এবং কালে মহাবিশ্ব পরিক্রমণ -- কিন্তু তা পাঠক আলোচকের কল্পনাই। কবির রচনায় তার সামান্য ইঙ্গিত ও নেই ) কবিতাটা বলেনা....... জীবনের সব দেনা পাওনা ফুরিয়ে যাবার পরেও কবি আর বনলতা মুখোমুখি বসে রইলেন। আমি তো কোন ব্যক্তির আবেগ বা অনুভূতি দিয়ে এই কবিতার বক্তব্যকে গুছিয়ে বুঝতে পারিনা। আর বক্তব্যের খোঁজই যখন মিলল না, তখন তার ক্রমিকতাই বা বুঝবো কি করে? কবি শুরুতে হাঁটছিলেন -- এখন বসেছেন। কিন্তু জীবন ফুরিয়ে যাবার পর যে বসা, সে কি বসা? আর হাজার বছর ধরে যে হাঁটা সে কি হাঁটা
? না, সময়ের গতিরুদ্ধ করে জীবনের লেনদেন ফুরিয়ে অনুভব করা?...' ক্ষেত্রগুপ্ত। অবশ্য সমালোচনা করার দায় সমালোচকদের নিজস্ব। তবে এই উন্নাসিক বক্তব্য 'বনলতা সেন'কে অনবদ্য প্রেমের কবিতা বলতে আমার মত যারা উন্মুখ তাদের ওপর কোনই নঞর্থকপ্রভাব ফেলতে ব্যর্থ। এখানে কবি এবং কবি-কৃতীর যে আলোচনা তিনি করেছেন সমালোচনা-সাহিত্যে তার নীট ফল 'শূন্য'। (বিস্তৃত জানার জন্য 'ভারবি' প্রকাশনীর 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য সমগ্র' দেখুন।)
।। পাঁচ।।
উপসংহারে অপ্রাসঙ্গিক স্বগতোক্তি মনে হলেও সম্প্রতি প্রকাশিত একটি মতের সঙ্গে সহমত মনে হওয়াতে উচ্চারণ করা জরুরী : " বইয়ের শেষ লেখায় ঝলসে উঠেছে একটি মন্তব্য, ' সবাই জানে, শিল্পই বাঙালির ভবিষ্যৎ। উপরন্তু বাঙালি আজ বিশ্বচারী।' " মন্তব্যটি ঠিক সিদ্ধান্ত বাক্যের মতো উচ্চারিত আর উচ্চারিত বলেই বোঝা যাচ্ছে শেষ লেখার এই উচ্চারণ বেদনাবিহীন কশাঘাত। শিল্প ভবিষ্যৎ বিশ্বচারী বাঙালির হাতে কি থাকবে
তা অনাগত আগামীই বলবে, এখনো তার সম্বল পুরনো চাল -- ভাতে বাড়িয়ে বাঙালি করে খাচ্ছে। "(-- বিশ্বজিৎ রায় : বাঙালি সংস্কৃতির অন্তরমহলে: 'এই সময় '১২ই মার্চ ২০২৩) ভবিষ্যতে এরকম দ্বিতীয় বাক -প্রতিমা নির্মাণ আদৌ সম্ভব কিনা,তা ও ভেবে দেখার বিষয়।