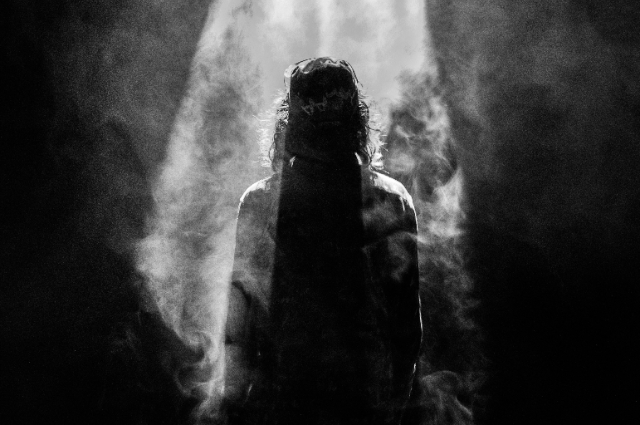
Photo by Mads Schmidt Rasmussen on Unsplash
ভূমিকা
‘পঞ্চভূত’’ পাঁচ বিস্মৃত মহারথীর জানা-অজানা কিছু কাহিনীর সংকলন। মহাভারত এবং পুরাণে বহু মহান রথী মহারথীদের ভিড়ে এই পাঁচ চরিত্র বভ্রুবাহন, বার্বারিক,বিকর্ণ, বিদুর ও পরশুরামের কাহিনী যতটা প্রকাশ পাওয়া উচিত ছিলো সেই মতো প্রচারের আলোয় আসেনি। ‘পঞ্চভূত’ আমার সীমিত জ্ঞানে বিস্মৃতির আড়ালে থাকা এই পাঁচ বিশ্রুতের বিস্মৃত কর্মকাণ্ডের কয়েকটি কাহিনীর ওপর আলোকপাত করার একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা মাত্র। এই প্রচেষ্টা যদি পাঠকমহলে সমাদৃত হয় তাহলেই লেখকের শ্রম সার্থক হ’বে এবং সেখানেই লেখকের প্রাপ্তি ও পরিতৃপ্তি।
(মহাভারতের পাঁচ ব্যতিক্রমী চরিত্র)
বভ্রুবাহন
গোড়ার কথা
এই কাহিনীর শুরু হয়েছে মহাভারতের ধর্ম যুদ্ধে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠার পর যখন মহারাজ যুধিষ্ঠির বসেছেন সিংহাসনে। এবার তার রাজাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজ চক্রবর্তী হওয়ার বাসনা হোলো। এটাই তো স্বাভাবিক। অশ্বমেধ যজ্ঞ সাফল্যের সাথে সম্পন্ন করতে পারলে তবেই না রাজ চক্রবর্তী হওয়া যায়। তাই মহারাজ যুবিষ্ঠির স্থির করলেন তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করবেন। এই কথা তিনি বাকি চার ভাই ভীম,অর্জুন,নকুল ও সহদেবকে জানালেন। তারাও মহারাজ যুধিষ্ঠিরের
এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছিলেন। এই অশ্বমেধ যজ্ঞ হোলো বৈদিক ধর্মের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজকীয যজ্ঞ। এই যজ্ঞে ঘোড়া বলি দেওয়া হোতো। প্রাচীন ভারতের রাজরাজরারা তাঁদের সাম্রাজ্যের সার্বভৌমত্ব প্রমাণ করার জন্য এই যজ্ঞের আয়োজন করতেন।
এই যজ্ঞের আয়োজন বসন্তকালের ফাল্গুন মাসের অষ্টমী অথবা নবমী তিথিতে করা হোতো। এই যজ্ঞের জন্য রাজার যোদ্ধাদের সাথে থাকা একটি সুলক্ষণ ঘোড়াকে এক বছর সময় ঘুরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেওয়া হোতো। সেই ঘোড়া যদি অন্য রাজ্যে বিচরণ করে এবং সেই রাজ্যের রাজা তা বন্ধ করে দেয় তবে তাঁদের যুদ্ধ করতে হোতো।
এই যুদ্ধে সফল হওয়া রাজা মহাশক্তিশালী হিসেবে স্বীকৃতি পেতেন।
এককথায় রাজ্য পালন,রাজ্যের সীমা বাড়ানো ও রাজ্যের উন্নয়নের অঙ্গ ছিল এই অশ্বমেধ যজ্ঞ।
কারণ রাজ্যের সীমা বাড়লেই পূজার সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং সাথে সাথে রাজ্যের কর ধার্য ও বেড়ে যাবে আর রাজ্যের কোষাগার ও ফুলেফেঁপে উঠবে। তাই এই অশ্বমেধ যজ্ঞকে এক সুদূরপ্রসারী উন্নত ভবিষ্যতের সোপানো বলা যেতে পারে। যাইহোক এই কাহিনী শুরু করার আগে আরও কিছু জানা অজানা তথ্য দেওয়া অবশ্য প্রয়োজন।
মহাভারতের কাহিনীতে মধ্যমপান্ডব ভীমের পুত্র ঘটোৎকচ এবং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের পুত্র অভিমন্যুর নাম বহুল চর্চিত। কিন্তু অর্জুন ও মনিপুর রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার পুত্র বভ্রুবাহন রয়ে গেছেন ইতিহাসের ধূসর পাতায় বিস্মৃতির অন্তরালে। তবুও ভীমের প্রপৌত্র বার্বারিকের নামে
‘খাটুশ্যাম’মন্দির আছে রাজস্থানের শিখর জেলায় এবং তিনি দেবতা হিসেবে সেখানে আজও পূজিত হয়ে থাকেন। কিন্তু বভ্রুবাহনের কথা তেমন করে শোনা যায় না। মহাভারতের একটি অন্যতম মুখ্য চরিত্র তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনের চারজন স্ত্রী ছিলেন দ্রৌপদী, উলুপী, চিত্রাঙ্গদা এবং সুভদ্রা। রিচার্জ স্পীড থেকেই তার চারটি পুত্র ছিল শ্রুতকর্মা,
ইরাবন, বভ্রুবাহন এবং অভিমন্যু। প্রথম নির্বাসনের সময় তিনি উলুপী, চিত্রাঙ্গদা এবং শ্রীকৃষ্ণের বোন সুভদ্রাকে বিবাহ করেছিলেন। এদের মধ্যে উলুপী ছিলেন নাগরাজ কৌরব্য ও বিষবাহিনীর কন্যা এবং তার পিতা গঙ্গা নদীর জলভাগের সর্পরাজ্যের শাসন করেছিলেন। উলুপী ছিলেন একজন প্রশিক্ষিত যোদ্ধা। ঠিক তেমনি চিত্রাঙ্গদা ছিলেন তৃতীয় পান্ডব অর্জুনের
তৃতীয় পত্নী। তিনি ছিলেন মণিপুরের রাজা চিত্রবাহন ও বসুন্ধরার কন্যা। মনিপুর রাজ চিত্রবাহনের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন চিত্রাঙ্গদা। একাধিক প্রজন্মের জন্য রাজবংশের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না, এবং যেহেতু চিত্রবাহনের কোন উত্তরাধিকারী ছিল না তাই তিনি চিত্রাঙ্গদাকে যুদ্ধ ও রাজ্য শাসনের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন। চিত্রাঙ্গদা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি তাঁর দেশের মানুষকে রক্ষা করার দক্ষতা অর্জন করেছিলেন।
অর্জুনের সাথে রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার বিবাহ
নির্বাসন কালে বহু রাজ্য ঘুরে মণিপুরে এসে উপস্থিত হন অর্জুন। এদিকে রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা সবসময় পুরুষ যোদ্ধার বেশেই থাকতেন। অর্জুন কামরূপ কামাখ্যার মন্দিরের কাছে শিকার করতে গেলে রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা অর্জুনের পথ আগলে দাঁড়িয়ে পড়েন এবং অর্জুনের শত অনুরোধেও তিনি পথ ছাড়েন না। তখন দু’জনে শুরু হয় ভয়ংকর যুদ্ধ। এদিকে যুদ্ধ করতে করতে অর্জুনের একটা তীরের ঘায়ে রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার চুলের বাঁধন খুলে যায়। বেরিয়ে পড়ে রাজকুমারীর আসল পরিচয় যে তিনি পুরুষ নন একজন নারী। তখন অর্জুন নিজেই যুদ্ধ থামিয়ে লজ্জা পেয়ে চিত্রাঙ্গদার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন একজন নারীর সাথে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণে। এবার অর্জুন চিত্রাঙ্গদার সততা ও স্বাভাবিক কারণে মনিপুর রাজকুমারীর প্রেমে পড়ে যান। যখন তিনি রাজা চিত্রবাহনের কাছে রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদার পাণি গ্রহণের জন্য প্রার্থনা করেন তখন রাজা তাকে তার পূর্বপুরুষ
প্রভন্জনার কাহিনী শোনান যিনি নিঃসন্তান ছিলেন এবং সন্তান লাভের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিলেন। অবশেষে দেবাদিদে মহাদেব প্রভন্জনার কাছে আমি ভূতন এবং তাকে বর দেন যে তার বংশের প্রতিটি উত্তরসূরীর একটি করে সন্তান হবে। যেহেতু চিত্রবাহন তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকে ভিন্ন তার পুত্র সন্তান ছিল না একটি কন্যা ছিল শুধু। ইনি তার প্রজাদের রীতি অনুযায়ী তাকে ‘পুত্রিকা’ বানিয়েছিলেন। এর অর্থ হল যে তার জন্ম দেওয়া একটি শিশু তাঁর উত্তরসূরী হবে অন্য কেউ নয়।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ যাওয়ার পর পঞ্চপান্ডবদের মধ্যে অলিখিত চুক্তি হয়েছিলো। যখন এক পাণ্ডব দ্রৌপদীর সাথে সহবাস করার সময় অন্য পাণ্ডব ভ্রাতার সেই সময় প্রবেশের অধিকার থাকবে না। আর শর্ত লঙ্ঘন করলে তাকে বারো বছর নির্বাসনে যেতে হবে।পঞ্চপান্ডবদের সবাই এক কথায় এই শর্তে রাজি হয়ে যান।কিন্তু একদিন জ্যেষ্ঠ পান্ডব যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর সাথে সহবাস করার সময় অর্জুন ভুলবশত সেই ঘরে ঢুকে পড়েছিলেন। তাই তাঁকে দীর্ঘ বারো বছরের জন্য নির্বাসনে যেতে হয়েছিলো। এই নির্বাচনকালে অর্জুন মনিপুর রাজ্যে এসে পৌঁছান এবং একদিন শিকার করার সময় তার রাজকুমারীদের সাথে মুখোমুখি সংঘাত হয়।
চিত্রাঙ্গদার মানিকগঞ্জ করে তিনি তিন বছর তাঁর সাথে মণিপুরে ছিলেন। চিত্রাঙ্গদা যখন একটি পুত্রের জন্ম দিয়েছিলেন তখন অর্জুন সেই পুত্রকে পিতৃ স্নেহে আলিঙ্গন করেছিলেন। তিন বছর পর তিনি চিত্রাঙ্গদাকে ছেড়ে চলে যান এবং হস্তিনাপুরে ফিরে আসেন। অর্জুন রাজকুমারী চিত্রাঙ্গদা কে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি তাকে তাঁর রাজ্যে ফিরিয়ে নেবেন। পিত্রাঙ্গদা তার ছেলে বভ্রুবাহনকে লালন পালন শুরু করেন। মহাভারতের চিত্রাঙ্গদা এবং তার রাজ্য সম্পর্কে কয়েকটি অধ্যায় উল্লেখিত আছে। অন্যদিকে পাণ্ডবরা বিভিন্ন অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়ে অবশেষে কৌরবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরে রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেন। তখন তাঁর মন অস্থির ছিলো কারণ যুদ্ধের সময় তাঁর নিজের আত্মীয়-স্বজনদের হত্যা করতে তার সর্বদাই খারাপ লাগতো। শিশুদের পরামর্শ মেনে তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ পরিচালনা করেন যেখানে একটি সুসজ্জিত ঘোড়া দেশ জুড়ে পাঠানো হ’বে এবং যেখানেই এটি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অতিক্রম করবে যে রাজা এটি পাঠিয়েছিলেন তিনি সেই জমি অধিগ্রহণ করবেন। সেইমতো অর্জুনকে ঘোরার যত্ন নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিলো। ঘোড়াটি উত্তর পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় এক সদ্য যুবক অর্জুনের বিরোধিতা করে। অর্জুন সেই যুবকের পরিচয় জানতে চাইলে সেই যুবক তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি দেশের রাজপুত্র এবং যুদ্ধ শুরু করার জন্য এই ভূমিকাই যথেষ্ট। তবুও অর্জুন সেই যুবককে অশ্ব ছেড়ে দেওয়ার জন্য বারবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সেদিন সেই যুবক বভ্রুবাহন ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিনা যুদ্ধে তিনি সেই ঘোড়াকে একপা ও এগোতে দেবেন না এমনই ধনুর্ভাঙ্গাপণ করে বসেছিলেন তিনি। নিয়তির কি নিষ্ঠুর রসিকতা যেখানে অর্জুনের মতো মহাধনুর্ধর পিতা ছিলেন পুত্র বভ্রুবাহনের কাছে শুধুই এক অপরিচিত যোদ্ধা মাত্র।
গঙ্গার অভিশাপ
এই কাহিনী বলার আগে চলে যেতে হ’বে মহাভারতের একেবারে সূচনাতে যেখানে মহারাজ শান্তনুর দুই পত্নী প্রথম পত্নী হলেন গঙ্গা এবং দ্বিতীয় পত্নী সত্যবতী। এই প্রথম পত্নী গঙ্গার পুত্র ছিলেন ভীষ্ম যিনি মহাভারতের ভীষ্ম পিতামহ নামে সুবিদিত এবং ন্যায় ও নিষ্ঠার প্রতীক। তাঁর আসল নাম ছিল দেবব্রত এবং তিনি স্বর্গ, মর্ত এবং পাতাল এই তিন লোককে সাক্ষী রেখে আজীবন কৌমার্যের ভীষণ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বলে তার নাম হয় ভীষ্ম এবং এই নামেই তিনি মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্র গুলোর অন্যতম।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দশম দিন পর্যন্ত তিনিই ছিলেন কোন পক্ষের প্রধান সেনাপতি। তিনি একাই পাণ্ডব পক্ষকে নাস্তানাবুদ করে চলেছিলেন। উপায়ান্তর না দেখে প্রিয় সখা শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে অর্জুন ছলনার আশ্রয় নেন ভীষ্মকে বধ করার জন্য।
সেই ধর্মযুদ্ধের দশম দিনে যখন অর্জুন পিতামহ ভীষ্মের সম্মুখীন হন তখন অর্জুন তাঁর রথে শিখন্ডীকে সারথী করেন কৃষ্ণের উপদেশ মেনে। বিসমিল্লাহ প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি কোন নারী বা নপুংসকের সাথে যুদ্ধ করবেন না। পন্ডি ছিল নপুংসক এবং তিনি ছিলেন পূর্বজন্মের অম্বা। পিছন দিকে দেখামাত্র ভীষ্ম তাঁর অস্ত্র ত্যাগ করেন। আর ঠিক তখনই কপটতার আশ্রয় নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন পিতামহ ভীষ্মকে একশোটি তীরে বিদ্ধ কোরে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাঙ্গনে শরশয্যায় শুইয়ে দেন।
এই খবরদার আশ্রয় নেওয়ার জন্য মঙ্গল পুত্র সপ্তবসু ক্ষোভের আগুনে ক্রুদ্ধ হ’য়ে মা গঙ্গা কে এর বিহিত করতে বলেন কারণ পিতামহ ভীষ্ম ছিলেন অষ্টবসুর এক বসু। মা গঙ্গা অষ্টবসুকে প্রতিশ্রুতি দেন কপটতার আশ্রয় নিয়ে ভীষ্মকে বধ করার ফল অর্জুনকে পেতেই হবে। সেই সেই কারণে মা গঙ্গা স্বপ্তবসুদের বলেন
“অর্জুনকে একবার নরক দর্শন করতে হ’বে এবং তাঁর ছেলের হাতেই মৃত্যু হ’বে মহা ধনুর্ধর অর্জুনের।” অর্জুন ছিলেন ভীষ্মের সবচেয়ে আদরের পৌত্র এবং সেই কারণেই এটা ছিল মা গঙ্গার অর্জুনের প্রতি অভিশাপ।
সম্মুখ সমরে পিতা পুত্র
যখন অষ্টমীদের ঘোড়াকে আটকে দিয়েছিলেন মনিপুরের রাজকুমার
বভ্রুবাহন তখন অর্জুন তাকে বারবার বলেছেন“পথ ছাড়ো হে বালক বাঁধা দিও না অশ্বকে এযে ধর্মরাজের অশ্বমেধের ঘোড়া, তুমি তো জানোনা তা।”
কিন্তু কে শোনে কার কথা। বভ্রুবাহন সেদিন চূড়ান্ত অবুঝ। আর হ’বে নাই বা কেনো সেও যে অস্ত্র চালনায় পারদর্শী যাঁকে
অস্ত্রশিক্ষা দিয়েছেন নাগ কন্যা উলুপী স্বয়ং।
সুতরাং ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হোলো দু’জনের। আড়াল থেকে মা চিত্রাঙ্গদা দেখে তো প্রমাণ গোনেন। দেখেন আর মনে মনে বলেন “এযে ভীষণধর্ম সংকট পিতা পুত্র কেউ যে চেনে না কাউকে।” অন্যদিকে যুদ্ধ ভীষণ রূপ নেয়। এবার কামাখ্যা দেবীর মন্ত্রপুতঃ তীর চালায় বভ্রুবাহন। অর্জুনের মাথা কেটে আলাদা হয়ে যায়। তাঁর অচেতন মুন্ডহীন দেহ লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। আর তা দেখে বভ্রুবাহনও অচৈতন্য হ’য়ে লুটিয়ে পড়েন মাটির ওপরে অর্জুনের পাশে। এই দৃশ্য দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন সেদিন। খবর পেয়ে উলুপিও হাজির হয়েছিলেন সেখানে। তিনি চিত্রাঙ্গদাকেকে অনেক কোরে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন সেদিন। তিনি তাঁর সাধ্যমতচেষ্টা করেছিলেন শান্ত করার। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা সেদিন ছিলেন অনড় সাফ্ জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি উলুপীকে “হয় অর্জুন প্রাণ ফিরে পিবে আর তা নাহ’লে তিনিও চিতায় উঠবেন অর্জুনের সাথে।”
এবার উলুপী বাঁচিয়ে তোলেন মন্ত্রপুতঃ মোতির স্পর্শে মৃত অর্জুনকে। জোড়া লাগে খণ্ডিত মুন্ডু এবং অচৈতন্য অর্জুনের দেহের। অর্জুন চোখ খোলেনো এবং বভ্রুবাহনও মন্ত্রপুতঃ জলের স্পর্শে জ্ঞান ফিরে পান। এরপর অর্জুন চিত্রাঙ্গদা কে নিয়ে আসেন হস্তিনাপুরে এবং কালে কালে চিত্রাঙ্গদাই হয়ে ওঠেন মাতা গান্ধারীর সেবা দাসী। আর মনিপুর রাজ্যের সিংহাসনে বসেন
বভ্রুবাহন। তিনি কখনোই হস্তিনাপুরে আসেননি।
অবশ্য মৃত অর্জুনকে বাঁচানোর অন্য কাহিনীও আছে। যে কাহিনীতে আছে অর্জুনের মস্তক ধর থেকে আলাদা হয়ে যাওয়ার পর সেই কাঁটা মস্তক নিয়ে অশ্বথামা পালিয়ে যাওয়ার পথে শ্রীকৃষ্ণ সেই মস্তক ছিনিয়ে নেন এবং এবং অর্জুনের ধড়ের সাথে সেই মস্তক জুড়ে দেন তিনি।
এই বীরযোদ্ধা বভ্রুবাহনের কাহিনী ধূসর অতীতের আড়ালেই রয়ে
গ্যাছে আজও।
বার্বারিক
মহাভারতের এক অনন্য বীরের কাহিনী
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, ধনুর্ধর অর্জুন, পিতামহ ভীষ্ম,দানবীর কর্ণ এবং মহাবলী ভীমসেনের নাম আজও মানুষের মনে গেঁথে আছে। এটাই স্বাভাবিক কিন্তু এক অনন্য বীর যোদ্ধার কথা আজও রয়ে গেছে ধূসর অতীতের বিস্মৃতির আড়ালে। এই অনন্য বীর যোদ্ধার নাম
বার্বারিক। তিনি কখনোই তেমন ভাবে প্রচারের আলোয় স্বমহিমায় প্রকাশ পাননি। পর্দার আড়ালে প্রায় বিস্মৃতই থেকে গেছেন তিনি।
স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জানতেন তার বিরক্তের মহিমা।
সেই বার্বারিক ছিলেন মধ্যম পান্ডব ভীমসেনের পৌত্র এবং বিরাটাকায় ঘটোৎকচের পুত্র। যে ঘটোৎকচ প্রকৃতিতে ছিলেন অর্ধ রাক্ষস এবং অর্ধ মানবের সংমিশ্রণ। কারণ ঘটোৎকচের মা হিরিম্বা ছিলেন প্রকৃতিতে এক যুদ্ধবাজ রাক্ষসী। ঘটোৎকোচের বিবাহ হয়েছিল নাগরাজ বাসুকীর কন্যা আহিলাবতীর সাথে। আহিলাবতী মৌরভী ও
কামবানথিকা নামেও পরিচিত ছিলেন। ফলে বার্বারিক প্রকৃতিতে ছিলেন অর্ধ মানব সিকিভাগ যক্ষ এবং সিকিভাগ রাক্ষস।
এই ভাবেই শুরু হয়েছে অকথিত কিংবদন্তি বীরযোদ্ধা বার্বারিকের কাহিনী। শৈশব থেকেই তিনি খুব সাহসী বীর যোদ্ধা ছিলেন। তাঁর মূল যুদ্ধবিদ্যার শিক্ষা হয়েছিলো মা আহিলাবতীর কাছে। আহিলাবতী ছিলেন একজন যুদ্ধ বিশারদ নারী। এটাই বার্বারিকের প্রাথমিক পরিচয় যিনি ছিলেন সমতার প্রতীক।বার্বারিকের যুদ্ধের মূল নীতিই ছিলো যুদ্ধক্ষেত্রে সবলের বিপক্ষে দুর্বলের পক্ষ নেয়া। এইভাবেই ক্রমাগত পক্ষ পরিবর্তনের নীতিতে বিশ্বাসী ছিলো বার্বারিক। তার এই দদুল্যমানতা চলতেই থাকতো যতক্ষণ না সে একাই যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে থাকতো। আর এটাই মূল কারণ ছিল বার্বারিকের এক বীর যোদ্ধা হয়েও মহাভারত মহাকাব্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অকথিত হয়ে পর্দার আড়ালে বিস্মৃতির অন্তরালে থাকার মূল কারণ।
বাল্যকালেই বার্বারিক কঠিন সাধনা করে দেবাদিদেব মহাদেবকে তুষ্ট করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ অব্যর্থ বাণের বরদান পেয়েছিলেন যাকে এক কথায়
‘তীন বাণ’ নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। ভগবান শিব তাঁকে একটি ধনুকও বরদান করেছিলেন যা তাকে অজেয় করে তুলেছিলো। সেই তিনটে তীর তিন ধাপে প্রয়োগ করা হতো। প্রথম তীরটি তাঁর লক্ষ্যবস্তুকে চিহ্নিত করতো। দ্বিতীয়টি চিহ্নিত করতো সে যে লক্ষ্যবস্তুকে রক্ষা করতে চায় করতে চায় এবং তৃতীয় তীরটি সব লক্ষ্যবস্তুকে ধ্বংস করে দিত যা প্রথম তীরটি চিহ্নিত করেছিল এবং যা দ্বিতীয় তীরটি রক্ষা করার জন্য চিহ্নিত করেনি।বার্বারিক তার মা মৌরভির কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলো যে সে সর্বদাই দুর্বলের পক্ষে যুদ্ধ করবে। মা মৌরভী ছিলেন বার্বারিকের প্রথম শস্ত্রগুরু যে তাঁকে যুদ্ধের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রশিক্ষিত করে তুলেছিলো।
আগের জন্মে বার্বারিক ছিলো একজন যক্ষ, যে কিনা আগ বাড়িয়ে দেবতাদের সভায় বলেছিলো”ভগবান বিষ্ণুকে পৃথিবীতে অধর্মকে নাশ করার জন্য অবতার হয়ে জন্ম নেওয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।সে একাই যথেষ্ট আমায় পৃথিবীর বুক থেকে অদম্যকে বিনাশ করার জন্য।”
এ কথা শুনে সৃষ্টিকর্তা ব্রম্মা, ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে এই বলে অভিশাপ দেন যে ভগবান বিষ্ণু যখন পৃথিবীতে আসবেন তিনি সব অশুভ শক্তির বিনাশের আগে সবার প্রথমে তাকেই বিরাজ করবেন। সেই যক্ষই বার্বারিক রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।
বার্বারিক যখন পাণ্ডব এবং পুলকদের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রস্তুতির কথা জানতে পারলো তখন সে তার মায়ের কাছে সেই যুদ্ধে সাক্ষী থাক আর ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলো। কিন্তু কুরুক্ষেত্রের রওনা হওয়ার আগে সে মাৌরবীর কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল সময়ের বহমানতার সাথে যখনই প্রয়োজন হবে সে দুর্বলের সহায়তা করবে যারা যুদ্ধে হারের দোরগোড়ায় আছে।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধ কতদিন স্থায়ী হ’বে সে বিষয়ে যথেষ্টই দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন। ইনি প্রথমে কৌরব পক্ষের প্রধান সেনাপতি ভীষ্মের কাছে জানতে চাইলেন কতদিন স্থায়ী হবে এই যুদ্ধ উত্তরে তিনি বলেন কুড়ি দিন, বলেছিলেন তিনি প্রতিপক্ষকে পঁচিশ দিনে ধ্বংস করে দেবেন এবং সবার শেষে কর্ণের উত্তর ছিল চব্বিশ দিন। এরপর তিনি পাণ্ডব পক্ষের অর্জুনকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন আটাশ দিন লাগবে যুদ্ধ শেষ করতে। মহারথীদের এইসব উত্তরের কারণে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ খুবই দুঃশ্চিন্তায় ছিলেন। কেননা তিনি জানতেন এই ধর্মযুদ্ধ যতদিন স্থায়ী হবে প্রাণহানি তত বেশি হ’বে।
বার্বারিক ও শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ
বারবারিকের কুরুক্ষেত্রে আগমনের সংবাদ যখন শ্রীকৃষ্ণ জানতে পেরেছিলেন তখন তিনি এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে বার্বারিকের মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রথম আলাপের পর তিনি বারবারিককে সেই একই প্রশ্ন করেছিলেন যা তিনি ওরব এবং পাণ্ডব পক্ষের মহারথীদের করেছিলেন। আর সেই প্রশ্নের তাৎক্ষণিক উত্তর দিয়েছিলেন বার্বারিক “এক মিনিট মাত্র”।
বার্বারিকেথ এই তাৎক্ষণিক উত্তর শুনে শ্রীকৃষ্ণ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন“এক মিনিটে কিভাবে সম্ভব বলো তুমি?”
উত্তরে বার্বারিক তাঁর গোপন কথা প্রকাশ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের কাছে। তার দেবাদিদেব মহাদেবের কাছ থেকে তিনবার প্রাপ্তির কথা জানিয়েছিলেন এবং এও বলেছিলেন এই তিন তীরের একটাই যথেষ্ট বিপক্ষের সবাইকে ধ্বংস করার জন্য।
তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কাছে সবকিছু বিশদে জানতে চেয়েছিলেন।বার্বারিক উত্তরে বলেন প্রথম তীরটির প্রয়োগ হয় বিপক্ষকে চিহ্নিত করার জন্য আর দ্বিতীয় তীরটি চিহ্নিত করে তিনি যা রক্ষা করতে চান এবং তৃতীয় তীরটি যা তিনি ধ্বংসের জন্য চিহ্নিত করেছেন এবং সব ধ্বংস করে সেই তিনটি তীর আবারও তারই তূণীরে যথাস্থানে ফিরে আসে।
শ্রীকৃষ্ণ ও ছাড়বার পাত্র ছিলেন না। তিনি প্রমাণ চাইলেন বল্লেন “আচ্ছা দেখাও দেখি তুমি যা বলছো তা সব সত্যি। তুমি সামনের ওই পিপল গাছের সব পাতাগুলোকে বেঁধে ফেলো দেখি তোমার ওই তিন বাণের ক্ষমতায়।”
চোখ বন্ধ করে বার্বারিক ধ্যানমগ্ন হ’য়ে একাগ্র মনে প্রথম তীরটি নিক্ষেপ করলেন প্রত্যেকটা গাছের পাতাকে চিহ্নিত করতে। আর ঠিক সেই সময় শ্রীকৃষ্ণ একটি পাতাকে তার পা দিয়ে ঢ়েকে দিলেন। প্রথম তীরটি এই পিপল গাছটির সমস্ত পাতাগুলোকে বেঁধে ফেলেছিল শুধু একটি পাতা ছাড়া যে পাতাটি ছিল শ্রীকৃষ্ণের পায়ের আড়ালে।
তাই তীরটি শ্রীকৃষ্ণের পায়ের চারপাশে ঘুরতে লাগলো। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ এরকম বিচিত্র দৃশ্য দেখে বিস্মিত হ’লেন অন্তিমি বার্বারিকের কাছে এর অন্তর্নিহিত কারণ জানতে চাইলেন। বার্বারিক সেদিন উত্তরে বলেছিলেন একটি পাতা নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণের পায়ের আড়ালে আছে এবং সেই কারণে
শ্রীকৃষ্ণকে তিনি সেই পাটি সরিয়ে নিতে অনুরোধ করেন না হলে তীরটি শ্রীকৃষ্ণের পায়ে আঘাত করবে।”
এই পরীক্ষার পর শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পেরেছিলেন
বার্বারিকের তিন তীর সত্যিই অব্যর্থ। শ্রীকৃষ্ণ তখন আপন মনে ভাবলেন যদি বার্বারিক গোলাপ দের পক্ষে এবং পান্ডবদের বিপক্ষে যুদ্ধে যোগদান করেন তা’হলে পান্ডবরা নির্ঘাত এই তিন তীরের থেকে নিজেদের আড়াল করতে পারবে না এবং পাণ্ডবদের পরাজয় হ’বে নিশ্চিত।
তখন শ্রীকৃষ্ণ বার্বারিককে প্রশ্ন করলেন “তুমি কোন পক্ষের হয়ে ধর্মযুদ্ধে যোগদান করবে কুরুপক্ষ না পাণ্ডবপক্ষ?”
বার্বারিক উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি তাঁর মায়ের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে পক্ষ যখন দুর্বল হবে তিনি তখন সেই পক্ষের হয়েই যুদ্ধে যোগদান করবেন। সেই কারণে যেহেতু পান্ডবরা কৌরবদের থেকে তুলনামূলকভাবে সংখ্যায় কম সৈন্যবলও অনেক কম এবং কৌরবদের থেকে পাণ্ডবরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল সেই কারণেই সে পান্ডব পক্ষে রয়েছে যুদ্ধে যোগদান করবে।
এই কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে, বার্বারিক নিজেও উপলব্ধি করতে পারেনি যে তাঁর যুদ্ধনীতি কি রকম জটিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ বার্বারিককে বলেছিলেন “তুমি যে পক্ষেই যোগদান করবে সেই পক্ষই বিজয়ী হবে। কিন্তু সমস্যা হোলো তুমি যদি পান্ডবদের যুদ্ধ কর তবে কৌরবরা দুর্বল হ’বে।
আবার যখন তুমি কৌরবদের হয়ে যুদ্ধ করবে তখন পাণ্ডবরা দুর্বল হয়ে পড়বে। এই কারণে তোমাকে বারবার পক্ষ পরিবর্তন করতে হবে কারণ তুমি তোমার মায়ের কাছে এই রকমই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।”
এরকমভাবে বারবার পক্ষ পরিবর্তনের দোদুল্যমানতার ফলে একসময় দেখা যাবে পান্ডব এবং কৌরব পক্ষের সবাই ধ্বংস হয়ে গেল একমাত্র তুমি একাই যুদ্ধক্ষেত্রে উত্তরজয়ী হয়ে আছো।”
এবার ব্রাহ্মণরূপী শ্রীকৃষ্ণ বার্বারিকের কাছে কিছু ‘দানভীক্ষা’ প্রার্থনা করলেন এবং বার্বারিকও এক কথায় শ্রীকৃষ্ণকে যেকোন দান দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এই দানের প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে
ব্রাহ্মণ রুপি শ্রীকৃষ্ণ বার্বারিকের মস্তক দান হিসেবে চেয়েছিলেন।
এই ধানের আর্জি শুনে বার্বারিক হতবাক হয়ে গেলেন। এবার তিনি সেই ব্রাহ্মণের আসল পরিচয় জানতে চাইলেন। শ্রীকৃষ্ণ বারবারিক এর কাছে ভগবান বিষ্ণুর স্বর্গীয় পবিত্র রূপে প্রকাশ হ’লেন।
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কেবলমাত্র দু’জন যোদ্ধাই
ভগবান বিষ্ণুকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তারা হ’লেন
তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন এবং মধ্যম পান্ডব ভীম সেনের পৌত্র বার্বারিক। ভগবান বিষ্ণুর স্বর্গীয় রূপের প্রকাশ প্রত্যক্ষ করে বার্বারিক তাঁর মস্তক শ্রীকৃষ্ণকে দান করতে সম্মত হয়েছিলেন।তবে সেই ত্যাগের আগে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে তার মনের ইচ্ছা পূরণের প্রতিশ্রুতি প্রার্থনা করেছিলেন যে তিনি যেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত সাক্ষী থাকতে পারেন।
শ্রীকৃষ্ণ বার্বারিকের শর্ত মঞ্জুর করে তাঁর খন্ডিত মস্তকটি একটি পাহাড় চূড়ায় স্থাপন করেছিলেন যাতে সে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করতে পারে।
কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল ঠিক আঠেরো দিন। যুদ্ধের শেষে পান্ডবরা নিজেদের মধ্যে তর্ক জুড়ে দেয় কে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা সেই প্রশ্ন নিয়ে। যখন তর্কের কোন সমাধান মেলেনা তখন পান্ডবরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। সব শুনে বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ তাঁর স্বভাব সিদ্ধ মৃদু হাসিতে উত্তরে বলেছিলেন “তোমরা বরং বার্বারিকের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চাও কেননা বার্বারিক ই এই কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একমাত্র সাক্ষী যে কিনা এই যুদ্ধকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছে।”
পান্ডবরা যখন বার্বারিককে
কে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা এই প্রশ্নের উত্তর জানতে চান তখন বার্বারিকের উত্তর ছিলো “দেখুন আমি এই যুদ্ধে শুধু দুটো জিনিসই প্রত্যক্ষ করেছি। এক সুদর্শন চক্র যুদ্ধক্ষেত্রের প্রতিটি কোনায় আবর্তিত হয়েছে এবং যারা অধর্ম এবং অন্যায়ের পক্ষে ছিল তাদের সবাইকে ধ্বংস করেছে আর অন্যদিকে প্রত্যক্ষ করেছি মা মহাকালী তাঁর লোলজিহ্বা দিয়ে অধর্মের পক্ষে যাঁরা যুদ্ধ করেছে তাদের রক্ত চেটে পৃথিবীকে পাপ মুক্ত করছেন।”
আসলে শ্রীকৃষ্ণের যুদ্ধনীতি এবং তাঁর উপস্থিতি পান্ডবদের যুদ্ধজয়ের মূল কারণ।
তখন পাণ্ডবরা বুঝতে পেরেছিলেন তাদের যুদ্ধজয়ের নেপথ্যে আসলে ছিলেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। পাণ্ডবরা শ্রীকৃষ্ণ কে প্রশ্ন করেন “কেন তিনি বার্বারিকের মস্তক দান হিসেবে চেয়েছিলেন?
শ্রীকৃষ্ণউত্তরে ব্রহ্মার সেই অভিশাপের কাহিনী বিশদে শুনিয়েছিলেন তাঁদের।বার্বারিকের আত্মত্যাগের প্রতিদান স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণও বার্বারিককে আশীর্বাদ করেছিলেন যে তার খন্ডিত মস্তক যেখানে স্থাপিত হয়েছে সেই অকুস্থলে তিনি ‘খাটুশ্যাম’ নামে পুজিত হবেন।
তাই আজও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদের ফলে বার্বারিক খাটুশ্যাম নামে পূজি হ’ন। রাজস্থানের শিখর জেলায়
খাটুশ্যামের মন্দির বিখ্যাত যার খুব কাছেই শ্যামজী আবির্ভূত হয়েছিলেন। একটু দূরেই শ্যামকুন্ড নামে একটি পুষ্করিণী আছে এবং ভক্তদের বিশ্বাস যে সেই পুষ্করিণীতে স্নান করলে রোগের উপশম এবং শরীর নিরাময় হয়।
এটাই মহাভারত মহাকাব্যের এক অখ্যাত যোদ্ধা বার্বারিকের কাহিনী যা আজও রয়ে গেছে পর্দার আড়ালে বিস্তৃতির অতলে।
বিকর্ণ
বিস্মৃতির অন্ধকারে
বিকর্ণ হ’লেন মহাভারত মহাকাব্যের তৃতীয় কৌরব যার পিতা ধৃতরাষ্ট্র এবং মাতা গান্ধারী।
মিছিলেন যুবরাজ দুর্যোধনের এক সহোদর ভাই। জ্যেষ্ঠ দুর্যোধন, মধ্যম দুঃশাসন এবং তৃতীয় কৌরব ছিলেন বিকর্ণ। তিনি সব সময় ধর্ম এবং ন্যায়ের পথে চলতেন। নাকি তিনি কোনদিনই প্রশ্রয় দেননি।
মহাভারত মহাকাব্যে তাই তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে বিকর্ণের কাহিনী। বিকনের পাঁচ জন স্ত্রী ছিলেন
ইন্দুমতি, সুদেষ্ণাবতী ,মৃদুলা ,বনজাক্ষী এবং সীমন্তিনী। তার দুই পুত্র সুকর্ণ এবং ত্রিকর্ণ
ও ষোলো জন কন্যা সন্তান ছিলো। পান্ডুবরা ছিল তার খুড়তুতো ভাই। গান্ধার রাজ শকুনি ছিলেন তাঁর মামা। যুযুৎসু ছিলেন তার সৎভাই।
বিকর্ণ ছিলেন অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের একজন শিষ্য, যিনি তীর ধনুক চালনায় অর্জুনের মতোই পারদর্শী ছিলেন। অস্ত্রশিক্ষা শেষ হ’লে
গুরু দ্রোণাচার্য যখন কৌরবদের বলেছিলেন গুরুদক্ষিণা হিসেবে পাঞ্চাল রাজ দ্রুপদকে বন্দী করে নিয়ে আসতে হ’বে তখন দূর্যোধন, দুঃশাসন,বিকর্ণ,এবং অন্য কৌরব ভাইয়েরা সৈন্যসহ পাঞ্চাল রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু সেই যুদ্ধে বিকর্ণ এবং তাঁর ভাইয়েরা পরাজিত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে পালাতে বাধ্য হয়েছিলেন।
মহসি ব্যাসদেবের আশীর্বাদে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর যে শতপুত্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে ধার্মিক ছিলেন এই বিকর্ণ। দুর্যোধনের ভাই হ’লেও তিনি তাঁর অন্য ভাইদের মতন বদমেজাজি ও অহংকারী ছিলেন না। তাই পাশা খেলায় পান্ডবদের পরাজয়ের পর হস্তিনাপুরের ভরা রাজ সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় একমাত্র প্রতিবাদ তিনিই করেছিলেন। আর সেই ঘটনার প্রতিবাদে একমাত্র তিনি সেদিন সভাস্থল পরিত্যাগ করেছিলেন। পরবর্তীতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধেও তিনি কৌরববদের হয়ে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করেছিলেন। মধ্যম পান্ডব ভীমসেন যখন কৌরবদের একশো ভাইকে বধ করার পণ নিয়ে কুরুক্ষেত্রকে পায় শ্মশানে পরিণত করেছেন তখন বিকর্ণ তার মুখোমুখি হয়ে দ্বন্দ্ব যুদ্ধের আহ্বান জানান। ভীম সেই মুহূর্তে কিছুক্ষণ ভাবেন এবং তার চোখের সামনে সেদিনের হস্তিনাপুরের ভরা রাজ সভায় দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সেই লজ্জাকর অপমানের দৃশ্য ভেসে ওঠে। সেদিনের সেই সভায় পিতমহ ভীষ্ম, অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য ,কৃপাচার্য এবং আরও অনেক রথী মহারথীর সেদিন উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেউই সেদিনকোন প্রতিবাদ করেননি দ্রৌপদীর সেই অপমানের। সবাই নিরবে সেই অন্যায়ের সাথে আপস করেছিলেন এবং চুপ থেকে সায় দিয়েছিলেন।
এইসব অতীতের কথা চিন্তা করে ভীম সেন যখন বিকর্ণকে বলেন “তুমিই একমাত্র মানুষ যে জানে ধর্ম কি? তুমি সরে দাঁড়াও আমি তোমাকে বধ করতে চাই না কারণ তুমিই একমাত্র মানুষ যে সেদিনের হস্তিনাপুরের
ভরা রাজ সভায় দুর্যোধনের দুষ্কার্যের প্রতিবাদ করেছিলে।”কিন্তু বিকর্ণ উত্তরে বলেছিলেন
“আজ আমার এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে যাওয়াটাই যে অধর্ম হবে এর মধ্যম পান্ডব। আমি এও জানি পুলকদের এই যুদ্ধে জয়লাভ কখনোই সম্ভব নয়। কারণ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব পক্ষে আছেন। কিন্তু আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্যোধনকে পরিত্যাগ করতে পারবো না। কারণ আমি ধার্মিক কিন্তু বিভীষণ নই। আর সেই কারণেই যে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।”তিনি এও বলেন “সেদিন সেই সভাস্থলে আমার যা কর্তব্য ছিল আমি তাই করেছি। কিন্তু এখন আমার কর্তব্য আমার ভাইদের রক্ষা করা তাই এসো আমার সাথে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ কর বৃকোদর ভীম।”
আর ভীমসেন ও বিকর্ণকে বধ করে করার পর সেদিন অঝোরে কেঁদেছিলেন।
বিকর্ণ ধর্মের পথে থেকেও কৌরবদের ভাই হওয়ার কারণে অধর্মের সাধ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। পান্ডবদের অজ্ঞাতবাসের সময় যখন কৌরবরা মহারাজ বিরাটের রাজধানী আক্রমণ করেছিল বিরাট রাজের ‘গোধন’ হরনের জন্য তখন বিকর্ণই বৃহন্নলার ছদ্মবেশী অর্জুনের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। যদিও সেই যুদ্ধে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন পরিশেষে এটাই বলতে হয় যে মহাভারতের বিকর্ণ হারিয়ে গিয়েছেন বিস্মৃতির অন্ধকারে।
পশুরাম
এক ব্যতিক্রমী চরিত্র
ভগবান বিষ্ণুর ষষ্ঠ অবতার ছিলেন পরশুরাম। তিনি ত্রেতা এবং দ্বাপর দুই যুগেই বর্তমান ছিলেন। পশুরাম যদিও মহাভারতের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি তবুও তিনি পরোক্ষভাবে মহাভারতের উপাখ্যানের সাথে জড়িয়ে আছেন। কারণ মহাকাব্য মহাভারতে তিনি ভীষ্ম,দ্রোণ এবং কর্ণের অস্ত্রগুরু ছিলেন। তিনি মহাভারত মহাকাব্যের এক অমর চরিত্র। পরশুরামের পিতা ছিলেন জমদগ্নি ঋষি তাই জন্মসূত্রে তিনি ব্রাহ্মণ যদিও তাঁর মা রেনুকা ছিলেন ক্ষত্রিয়।
কঠোর তপস্যা করে শিবের কাছ থেকে বর স্বরূপ পরশু অর্থাৎ কুঠার লাভ করেছিলেন তিনি এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেছিলেন। তাই পরশুরাম ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়। তিনিই ছিলেন প্রথম যোদ্ধা ঋষি।
মা রেনুকা ছিলেন অযোধ্যার সূর্যবংশের সন্তান। এই বংশেই পরে শ্রীরামচন্দ্রের জন্ম হয়। পরশুরাম ছিলেন শিবের উপাসক। একদিন নদীতে স্নানের সময় চিত্ররথ নামের এক রাজাকে স্বস্ত্রীক জলবিহার করতে দেখে পশুরামের মাতা রেনুকা কামাতুর হয়ে পড়েন। এই দৃশ্য দেখে ক্ষুব্ধ জমদগ্নি ঋষি পুত্রদেরকে মাতৃহত্যার আদেশ দেন। কিন্তু পাঁচ পুত্রের মধ্যে চার্য নিতে রাজী হননি। পিতার অভিশাপে তাঁরা নপুংসক হয়ে যান।
এই ঘটনায় দোটানায় পড়ে যান পরশুরাম। পিতার আদেশ পালন করবেন নাকি মাতৃহত্যার বোঝা বহন করবেন এই চিন্তায় পরশুরাম নিজের মায়ের কাছে সমস্ত কথা সবিস্তারে বলেন। কারণ শাস্ত্রে আছে মাতৃহত্যা যে মহাপাপ। পশুরামের মা রেনুকা ছিলেন সত্যপারায়ণ তাই তিনি ছেলেকে পিতার আদেশ রক্ষা করতে বলেছিলেন। পশুরাম তখন পিতার আদেশ পালন করতে কুঠার দিয়ে তাঁর মায়ের শিরোচ্ছেদ করেছিলেন।
মাতৃহত্যার পাপের ফলে তাঁর কাঁধ থেকে
আর সেই কুঠার নামেনি। এই পাপ ষ্খলনের জন্য তিনি তীর্থ থেকে তীর্থে ঘুরে বেড়ান এবং পরিশেষে রাজস্থানের চিত্তোর জেলার মাতৃকুন্ডিয়া নামক স্থানে পরশুরাম মাতৃহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন এবং এখানেই তিনি দেবাদিদেব শিবের তপস্যা করেছিলেন, এবং শিবের উপদেশেই তিনি মাতৃকুন্ডিয়ার জলে স্নান করে নিজেকে পাপ মুক্ত করেন।
পরশুরাম ও ক্ষত্রিয় নিধন
মহাভারত এবং পুরান অনুসারে সবচেয়ে বিখ্যাত ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন কার্তবীর্যার্জুন। সহস্র বাহু ছিলেন তিনি। তাকে সম্রাট চক্রবর্তীও বলা হোতো। ঋগ্বেদে কার্তবীর্যার্জুনের নামের উল্লেখ আছে। নাগা প্রধান কারকোটক নাগা থেকে নর্মদা নদীর তীরে মাহিষ্মতি শহর জয় করেন এবং এই শহরটিকে তার দুর্গ রাজধানী করেছিলেন তিনি। কার্তবীর্যাজুন হৈসে রাজ কৃতবীর্যের পুত্র ছিলেন। ঋষি দত্তাত্রেয়র আশীর্বাদে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সহস্রবাহু হওয়ার বরদান লাভ করেন। পুরাণের কাহিনী অনুযায়ী কার্তবীর্যাজুন এবং তার বাহিনী জমদগ্নি ঋষির কাছে অতিথি হয়েছিলেন। তখন ঋষি জমদগ্নি তাঁর রাজ অতিথি এবং সেনাবাহিনীকে তাঁর দিব্য কামধনুর নৈবেদ্য দিয়েছিলেন। প্রতিদানে রাজা কার্তবীর্যার্জুন নিজের প্রজাদের উন্নতির জন্য ঋষি জমদগ্নির আশ্রমের কামধেনু দাবি করে বসেন। কিন্তু জমদগ্নি ঋষি রাজার সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন কারণ তার ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য গরুর প্রয়োজন ছিলো। রাজা তার সৈন্যদের পাঠিয়েছিলেন গরু নিয়ে আসতে। ফলে ঋষি জমদগ্নি ও রাজা কার্তবীর্যার্জুনের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হ’লে রাজা মেজাজ হারিয়ে ঋষি জমদগ্নির মাথা কেটে ফেলেন। যখন পশুরাম আশ্রমে ফিরে এসে সব জানতে পারেন তখন প্রতিশোধের জন্য পরশুরাম রাজা কার্তবীর্যার্জুন এবং রাজার সমস্ত সেনাবাহিনীকে শিবের আশীর্বাদ ধন্য একটি রণতড়ি দিয়ে হত্যা করেছিলেন। এইভাবে পরশুরাম সমস্ত পৃথিবী জয় করেছিলেন এবং একুশ প্রজন্মের জন্য ক্ষত্রিয়দের এই নির্মূলের আইন করেছিলেন।
অন্য মতে কার্তবীর্যার্জুন সতেরো জন অক্ষৌহিনীকে একা পরশুরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু পশুরাম এককভাবে সমগ্র সৈন্য বাহিনীকে হত্যা করেছিলেন ও কাউকে জীবিত রাখেননি তিনি। কার্তবীর্যাজুন তার ঐশ্বরিক সোনার রথে এসেছিলেন যা ছিল বাধাহীন যে কোনও জায়গায় পৌঁছতে পারে। রাজা নিজেও একজন শক্তিশালী তীরন্দাজ ছিলেন। একই সাথে তিনি পাঁচশো ধনুক চালাতে পারতেন চালাতে এবং পাঁচশো তীর ছুঁড়তে সক্ষম ছিলেন।পরশুরাম রাজা কার্তবীর্যার্জুনের ধনুক ভেঙ্গে এবং তার ঘোড়া ও সারথিকে মেরে ফেলেছিলেন আর নিজের তীর দিয়ে সেই ঐশ্বরিক রথটিকেও ধ্বংস করেছিলেন। তখন রাজা পরশুরামকে বহু অস্ত্র,পাথর এবং গাছ ছুড়ে মেরেছিলেন। কিন্তু ভগবান পশুরাম এগুলোকে প্রতিহত করে তাঁর তীর দিয়ে কার্তবীর্যার্জুনের হাজার হাত কেটে কুঠার দিয়ে তাকে খন্ড করে দিয়েছিলেন। এইভাবে ভগবান পশুরাম পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়মুক্ত করেছিলেন।
পশুরাম ছিলেন অমর। তিনি হিন্দু ধর্মের কেন্দ্রীয় দেবতা ভগবান বিষ্ণুর দশ অবতারের মধ্যে ষষ্ঠ অবতার এবং তাকে চিরঞ্জীবীদের একজন বলে মানা হয়ে থাকে। পরশুরাম কৈঙ্কন ও মালাবার অঞ্চলকে সমুদ্রের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করেছিলেন। তিনি ছিলেন ব্রহ্মক্ষত্রিয়। পশুরামের আরো এক নাম হোলো জমজগ্ন্যা। যতদূর জানা যায় তিনিই ছিলেন প্রথম যোদ্ধা ঋষি।
বিদুর
পূর্বকথা
অণীমান্ডব্য ঋষিকে অকারণে শূলে চড়ানোর শাস্তি দেওয়ার কারণে তিনি যমরাজকে অভিশাপ দেন যে যমরাজ মর্ত্যে কোন মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করবেন। সেই কারণে যম বিদুর রূপে ব্যাসদেবের নিয়োগে এবং বিচিত্রবীর্যের প্রথমা স্ত্রী অম্বিকার দাসী পরিশ্রামী বা মর্যাদার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। অম্বিকার গর্ভে অন্ধ পুত্র এবং
অম্বালিকার গর্ভে পান্ডুবর্ণ পুত্রের জন্ম হ’লে
মাতা সত্যবতী তার গর্ভে আরও এক পুত্র উৎপন্ন করতে অম্বিকাকে ব্যাসদেবের আশ্রমে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু আশ্রমে যাওয়ার আগে ব্যাসদেবের বীভৎস কদর্য চেহারা মনে করে অম্বিকা আর ব্যাসদেবের আশ্রমে যেতে রাজি হ’লেন না। পরিবর্তে তিনি তাঁর এক দাসী পরিশ্রামীকে ব্যাসদেবের আশ্রমে পাঠালে ব্যাসদেব নিয়োগের মাধ্যমে সেই দাসীকে একমাত্র সন্তান দেন যার নাম রাখা হয়েছিলো বিদুর।
পিতমহ ভীষ্ম বিদুরকে সন্তান স্নেহে প্রতিপালিত করেন। ভীষ্মের তত্ত্বাবধানে বিদুর ধনুর্বেদ, গজ শিক্ষা, নীতিশাস্ত্র, ইতিহাস,পুরাণ প্রভৃতিতে সুশিক্ষিত হয়ে উঠেছিলেন। ব্রাহ্মণের ঔরসে শুদ্রা জননীর গর্ভে জন্মের কারণে রাজ্যে তার কোন অধিকার ছিলো না।
তিনি কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের মহামন্ত্রী ছিলেন। তিনি ধৃতরাষ্ট্রের অধর্মকে কখনোই প্রশ্রয় দেননি। দুর্যোধনের জন্মের সময় দুর্লক্ষণ দেখে ইনিই ধৃতরাষ্ট্রকে এই সন্তান পরিত্যাগ করতে বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই উপদেশে
ধৃতরাষ্ট্র কান দেননি। বিদুরের সহায়তাতেই পান্ডবেরা যতুগৃহ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন ধৃতরাষ্ট্র দ্রুপদ পুরী থেকে কুন্তী ও দ্রৌপদী সহ পঞ্চপান্ডবকে হস্তিনাপুরে ফিরিয়ে আনার জন্য বিদুরকেই পাঠিয়েছিলেন।
যুধিষ্ঠিরের সাথে শকুনির পাশা খেলাকে স্থগিত করার জন্য তিনি দুর্যোধনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্যোধন বিঁদুরের সেই পরামর্শে কর্ণপাত করেননি। বিদুরকে সবচেয়ে বিচলিত হতে দেখা গিয়েছিলো দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময়ে। তিনি মৌখিকভাবে এই কাজে বাধা দেওয়ার প্রবল চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন।পরে অবশ্য বিঁদুরের পরামর্শ মতো মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র এই বিবাদ মিটিয়েছেন। পান্ডবেরা বনবাসে গেলে ধৃতরাষ্ট্র ভয়ে তাঁর কাছে পরামর্শ প্রার্থনা করলে তিনি পান্ডবদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিদুরের সেই পরামর্শ ধৃতরাষ্ট্র গ্রহণ করেননি এবং বিদুরকে তিনি বলেছিলেন রাজ্য ছেড়ে পান্ডবদের কাছে চলে যেতে। তখন বিদুর মনের দুঃখে রাজ্য ছেড়ে পান্ডবদের কাছেই চলে গিয়েছিলেন। পরবর্তীতে ভীষ্মের উপদেশের ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাঠিয়ে বিদুরকে রাজ্যে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলেন।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের আগে তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে নানা রকম ভাবে যুদ্ধ করার সংকল্প থেকে বিরত থাকতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর তিনি পনেরো বছর ধৃতরাষ্ট্রের সাথে পাণ্ডবদের আশ্রয়ে বসবাস করেছেন। যুধিষ্ঠির তাঁকে কনিষ্ঠ পিতা বলে সম্বোধন করতেন যেহেতু বেলুর স্বয়ং সাব ভ্রষ্ট ধর্মরাজ আবার যুধিষ্ঠির নিজেও ধর্মপুত্র তাই অনেকেই বিদুরকে যুধিষ্ঠিরের পিতা বলে সম্বোধন করেছেন কারও কারও মতে বিদুর বনবাসী ভ্রাতা পান্ডুর পুত্র উৎপন্ন করতে দেবী কুন্তীর সাথে সহবাস করেন যার ফলে যুধিষ্ঠিরের জন্ম হয়েছিলো। ইনি ধৃতরাষ্ট্র এবং অন্যান্যদের সাথে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হন এবং সেখানেই তিনি যোগাসনে দেহত্যাগ করেন।
বিদুর কাহিনী একনজরে
যদিও মহাভারত মহাকাব্যের একটি অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র তিনি তবুও বিদুর সেই ভাবে প্রকাশের আলোয় আসেননি। বিদুর মহর্ষি ব্যাসদেব এবং পরিশ্রামী বা মর্যাদার সন্তান। পরিশ্রামী ছিলেন রানী অম্বিকার
হস্তপরিচারিকা। পরিশ্রামী ও মহর্ষি ব্যাসদেবের মিলনের মাধ্যমে বিদূরের জন্ম হয়েছিলো। বিদুর অত্যন্ত ধর্মশীল, বিচক্ষণ, ধীমান এবং দূরদর্শী ছিলেন। অম্বিকার গর্ভে অন্ধপুত্র এবং অম্বালিকার গর্ভে পান্ডুবর্ণ পুত্রের জন্ম হলে বেদব্যাস ও মাতা সত্যবতী বিচলিত হয়েছিলেন এবং সেই কারণে পরিশ্রামী বা মর্যাদাকে সক্ষম বংশধরের আশায় ব্যাসদেবের আশ্রমে পাঠিয়েছিলেন এবং পরিশ্রামীর স্বতঃস্ফূর্ত সাহচর্যের ফলস্বরূপ বিদুরের মতন একজন সর্বগুণান্বিত বংশধর লাভ করেছিলেন।
বিদুর মিথিলার রাজা সুদেবের শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভজাত কন্যা সুলভাকে বিবাহ করেছিলেন। সুলভা পরস্বী অথবা পরালরী নামেও পরিচিত ছিলেন। বিদুর ও সুলভার প্রথম বারো জন পুত্র নৃসিংহ, বামন, বিষ্ণু,অক্রুর, যদু, শংকর, মুরারী, মর্দন, আনন্দ, রামন,বিশ্ব ও রাঘব যমুনা তীরের কৃষক কন্যাদের বিবাহ করেন। এদের প্রত্যেকেরই দুইটি করে পুত্র সন্তান ছিলো। এরা সবাই আশ্রমে দেহত্যাগ করেন। বিদুরের অপর দুই পুত্র অন্যস্ব ও অনুকেতু পরীক্ষিতের সভাসদ হয়েছিলেন। কন্যা অম্বাবতি মানসুরের সাথে পালিয়ে বিবাহ করেছিলেন। তাদেরই কন্যা ঊষা শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধকে বিবাহ করেছিলেন।
যদিও বিদুরকে যুদ্ধাঙ্গনে দেখা যায়নি কিন্তু তার প্রধান অস্ত্র ছিল তীর ধনুক। সংস্কৃত ভাষায় বিদুর শব্দের অর্থ হলো দক্ষ,বুদ্ধিমান তথা জ্ঞানী। মহাভারত মহাকাব্যে বিদুর চরিত্রটিও অপেক্ষাকৃত অবহেলিত হয়ে আছে অন্য সব কেন্দ্রীয় চরিত্রের নিরীখে।
কৃষ্ণের দর্শন
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন অনুযায়ী বিদুরকে ধর্মরাজর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিলো।
যার অর্থ তিনি ছিলেন ধার্মিকতার রাজা। শ্রীকৃষ্ণ মানুষের কল্যাণে তাঁর ভক্তি এবং জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রে দক্ষতার জন্য বিদুরকে সম্মান করতেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন পান্ডবদের শান্তি দূত হিসেবে হস্তিনাপুরে গিয়েছিলেন তখন তিনি কৌরব দরবারে একমাত্র নিরপেক্ষ ব্যক্তি হওয়ার কারণে বিদুরের বাড়িতে থাকার পরিবর্তে রাজপ্রাসাদে থাকার জন্য দুর্যোধনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। দুর্যোধনের পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণ বিদুরের কক্ষে তাতে যাপন করেছিলেন।
কারণ তাঁর মাথায় যে চিন্তা চলছিল এবং বিদুর এবং দুর্যোধনের মধ্যে পার্থক্য ছিলো। আসলে দুর্যোধনের উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণের সাথে বিলাসিতা করা ও তাঁকে কৌরবদের পক্ষে যোগদান করতে রাজী করানো। দুর্যোধনের এই অভিপ্রায় টের পেয়ে তিনি দুর্যোধনের প্রস্তাব পত্রপাঠ প্রত্যাখান করেছিলেন। কৃষ্ণ জানতেন যে বিদুর ও তাঁর স্ত্রী যে খাবারটি তাকে নিবেদন করেছিলেন তা ছিল কোন অপ্রীতিকর উদ্দেশ্য ছাড়াই প্রেম ও স্নেহের মিশ্রণে নিবেদিত।
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ
মহাভারতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ আগে বিদুর মৃত্যু সম্পর্কে
ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ঋষি
সনৎসুজাত তাঁকে আহবান করেছিলেন।
শ্রীকৃষ্ণের সফরের সময় বিদূর বারবার সবাইকে বার্তাবাহকের কথায় মনোযোগ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর এইকারনে ক্রমাগত বিরক্ত হয়ে দুর্যোধন ক্রোধে ফেঁটে পড়েন এবং বিদুরের শূদ্রানী মাকে দোষারোপ এই বলে করেন যে কৌরবরা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছেন তাঁদের সাথে বিদুর বিশ্বাসঘাতকতা করছেন। এইসব মৌখিক আক্রমণের প্রতিবাদে বিদুর মহামন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে অংশ না নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তিনি তাঁর ধনুক ভেঙ্গে দিয়েছিলেন। মহাভারতের স্বল্প পরিচিত সংস্করণ গুলিতে বিদুরকে একজন সুদক্ষ তীরন্দাজ হিসাবে এমনও প্রশংসা করা হয়েছে যে তিনি যদি যুদ্ধে কৌরবদের পক্ষে অংশ নিতেন তবে পাণ্ডবরা চূর্ণ হয়ে যেতেন। কারণ বিদুরের ধনুকটি ভগবান বিষ্ণু নিজেই তৈরি করেছিলেন ও বিষ্ণুর আদেশেই তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো।
বিদুরের মৃত্যু
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর যুধিষ্ঠির সম্রাট হন এবং তাঁর অনুরোধে বিদুর প্রধানমন্ত্রীর পদে পুনর্বহাল হন। বহু বছর পর বিদুর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী এবং কুন্তীর সাথে যান যারা একটি সরল জীবন যাপনের জন্য বনবাসী হয়েছিলেন। সারথি সঞ্জয়ও তাঁদের সাথে ছিলেন। দু'বছর পরে যুধিষ্ঠির তাঁদের দেখতে বনে গেলে বিজুরের মৃতদেহ দেখতে পান। তুমি যখন সেই মৃতদের কাছে যান ইদুরের আত্মা যুধিষ্ঠিরের দেহে প্রবেশ করে এবং যুধিষ্ঠির বুঝতে পারেন যে তিনি এবং বিদুর একই সত্তা ধর্মের অনুসারী। দৈববাণী হয় যুধিষ্ঠিরকে বিদুরের মৃতদেহ দাহ না করার কথা বলে। যুষ্টিক বিদুরের দেহ কাঠের মধ্যে রেখে চলে আসেন।
বিদুর নীতি
বিদুর নীতিতে ব্যক্তিগত বিকাশের পরামর্শ এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তির বৈশিষ্ট্যসহ কয়েকশো শ্লোক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বিদুর পরামর্শ দিয়েছেন একজন জ্ঞানী ব্যক্তি রাগ,উল্লাস,অহংকার, লজ্জা ও মূর্খতা থেকে বিরত থাকুন। যার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস রয়েছে প্রতিকূলতা বা সমৃদ্ধি দ্বারা সে তাঁর নিজের প্রচেষ্টায় কখনোই বাধাগ্রস্ত হয় না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পূণ্য এবং লাভ মানুষ একসাথে পেতে পারে তাঁর সর্বোত্তম ক্ষমতা প্রয়োগ করে এবং কাজ করে। কোন কিছুকেই উপেক্ষা করে নয়। তিনি দ্রুত বুঝতে পারেন মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করেন। তিনি যা হারিয়েছেন তার জন্য কখনও দুঃখ করেন না এবং সংকটের সময় তিনি জ্ঞান হারান না। তিনি ক্রমাগত শিখেই চলেছেন। তিনি যা কিছু অনুভব করেন তার থেকে তিনি জ্ঞানের সন্ধান করেন। ইনি সিদ্ধান্তের পরে কাজ করেন এবং চিন্তা করার পরে সিদ্ধান্ত নেন। সে অহংকার বা অত্যাধিক বিনয়ের সাথে আচরণ করে না। সে কখনও অপরকে খারাপ কথা বলে না এমনকি নিজের প্রশংসাও করে না। সে নিজের সম্মানে উল্লাস করে না,
অপমানে দুঃখ করে না। গঙ্গা নদীর কাছে একটি শান্ত স্থির হ্রদের মতন অন্যরা তাঁর সাথে যা করে তাতে সে কখনোই বিচলিত হয় না।
উপসংহার
তাই থিওসফিক্যাল জগতে বিদুর মহাচোহন হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। মহাচোহনকে ট্রান্স হিমালয়ান রহস্যবাদীদের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাসের প্রধান বলা হয়ে থাকে। মহাভারতের বেশিরভাগ চরিত্রই ছিলো এক বা অন্য ঈশ্বরের পুনর্জন্ম। যেমন বিদুর নিজে ছিলেন ধর্মরাজের পুনর্জন্ম। এটি রামায়ণ এবং মহাভারত উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। বিদুর কে সত্য,কর্তব্য ,পরায়নতা,নিরপেক্ষ বিচার এবং অবিচল ধর্মের এক আদর্শ দৃষ্টান্ত হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। তিনি মহাভারতের অন্তর্নিহিত চেতনার এক মূর্ত প্রতীক।
